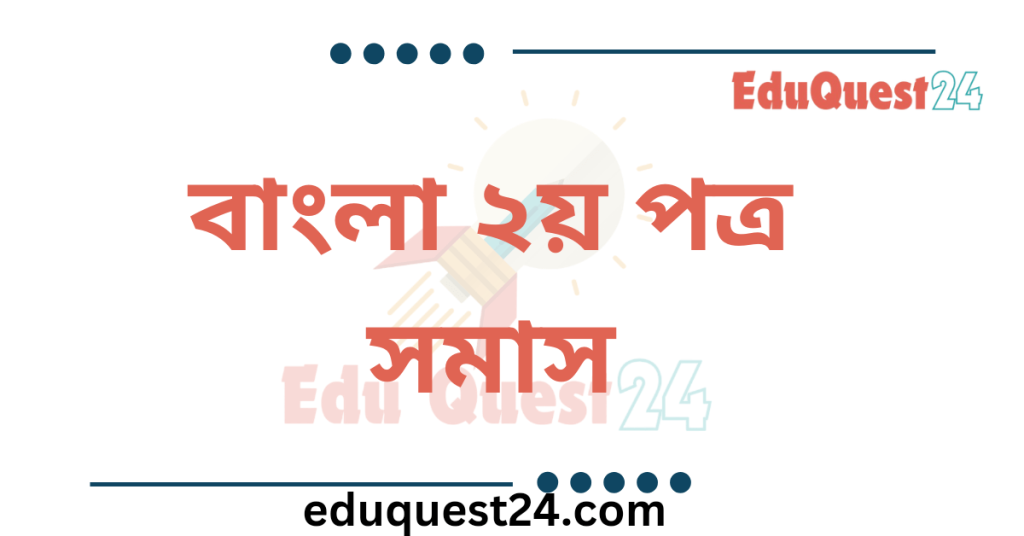সমাস কাকে বলে? সমাস হলো দুটি বা ততোধিক পদের সংক্ষিপ্ত রূপের মিলন। সমাসে একাধিক শব্দ একত্র হয়ে একটি শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং অর্থে সংকোচন ঘটে। নিচে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
সমাস কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি?
সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন:
দেশে সেবা = দেশসেবা
বই ও পুস্তক = বইপুস্তক
নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া।
সমাসের বৈশিষ্ট্য
১. পাশাপাশি দুই বা তার অধিক শব্দ থাকতে হবে।
২. এসব শব্দের মধ্যে অর্থসংগতি থাকতে হবে।
৩. এসব শব্দের মধ্যে বৃহৎ শব্দ তৈরির যোগ্যতা থাকতে হবে।
৪. নতুন শব্দ গঠন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৫. একাধিক শব্দকে সংকোচিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৬. শব্দগুলোর বিভক্তি লোপ পেতে হবে।
সন্ধি ও সমাস পার্থক্য
| সন্ধি | সমাস |
| ১। বর্ণের সাথে বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। | ১। শব্দের সাথে শব্দের মিলনকে সমাস বলে। |
| ২। সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে অবস্থিত। | ২। সমাস ব্যাকরণের রূপতত্ত্বে অবস্থিত। |
| ৩। সন্ধি ৩ প্রকার। যেমন: স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি। | ৩। যেমন: সমাস ৬ প্রকার। দ্বন্দ্বসমাস, দ্বিগুসমাস, কর্মধারয়সমাস, তৎপুরুষসমাস, অব্যয়ীভাবসমাস বহুব্রীহিসমাস। |
| ৪। সন্ধিতে বিভক্তি লোপ পায় না। | ৪। সমাসে অলুক বাদে অন্য সমাসের বিভক্তি লোপ পায়। |
| ৫। সন্ধিতে বর্ণে বর্ণে মিলন ঘটে। সন্ধিতে শব্দের মিলন বর্ণ ও উচ্চারণভিত্তিক। দুটি বর্ণের মিলন ঘটে। | ৫। সমাসে শব্দে শব্দে বা পদে পদে মিলন ঘটে। সমাসে শব্দের মিলন অর্থভিত্তিক। দুই বা দুয়ের অধিক শব্দের মিলন ঘটে। |
| ৬। সন্ধি অল্প সংখ্যক নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে। | ৬। সমাস অনেক নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে। |
| ৭। সন্ধির ফলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে না। | ৭। সমাসের ফলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। |
| ৮। সন্ধি শব্দকে গতিশীল করে। | ৮। সমাস বাক্যকে গতিশীল করে। |
| ৯। সন্ধির নমুনা হলো: বিদ্যা+আলয়-বিদ্যালয়, প্রতি+এক-প্রত্যেক, হিম+আলয়-হিমালয়। | ৯। সমাসের নমুনা হলো: বিদ্যার জন্য আলয়-বিদ্যালয়, একের পরে এক প্রত্যেক, হিমের আলয়-হিমালয়। |
| ১০। সন্ধি উচ্চারণকে পরিষ্কার করে। | ১০। সমাস বক্তব্যকে সুন্দর, শ্রুতিমধুর ও সংক্ষিপ্ত করে। |
১। সমস্ত পদ: সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদকে সমস্ত পদ বলে।
২। সমস্যমান পদ: সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদকে সমস্যমান পদ বলে।
৩। সমাসজাত শব্দ বা ব্যাসবাক্যের প্রতিটি পদকে সমস্যমানপদ বলে।
৪। সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ বা শব্দকে পূর্বপদ বলে এবং পরবর্তী অংশ বা শব্দকে উত্তরপদ বা পরপদ বলে।
৫। সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য: সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তাকে সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বলে।
সমাসের প্রকারভেদঃ
সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যেমন:
১। দ্বন্দ্ব সমাস
২। কর্মধারয় সমাস
৩। তৎপুরুষ সমাস
৪। বহুব্রীহি সমাস
৫। দ্বিগু সমাস
৬। অব্যয়ীভাব সমাস।
অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।
দ্বন্দ্ব সমাস
যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। অর্থাৎ, যে সমাসে সমাসবদ্ধ পদসমূহ সমান গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং তাদের মধ্যে ‘ও’, ‘এবং’, ‘আর’ এই অর্থ বোঝায়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন:
তাল ও তমাল = তাল-তমাল
দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম।
এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর – এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন:
১। জল + স্থল = জলস্থল (জল ও স্থল)
২। দিন + রাত = দিনরাত (দিন ও রাত)
৩। সুখ + দুঃখ = সুখদুঃখ (সুখ ও দুঃখ)
৪। রাম + শ্যাম = রামশ্যাম (রাম ও শ্যাম)
৫। কৃষক + শ্রমিক = কৃষকশ্রমিক (কৃষক ও শ্রমিক)
৬। শিক্ষা + দীক্ষা = শিক্ষাদীক্ষা (শিক্ষা ও দীক্ষা)
৭। সত্য + মিথ্যা = সত্যমিথ্যা (সত্য ও মিথ্যা)
৮। আনন্দ + বিষাদ = আনন্দবিষাদ (আনন্দ ও বিষাদ)
৯। জীবন + মরণ = জীবনমরণ (জীবন ও মৃত্যু)
টেকনিক: যদি দুই বা ততোধিক শব্দের মাঝে “ও”, “এবং”, “আর” যোগ করে অর্থ ঠিক থাকে — তাহলে সেটা দ্বন্দ্ব সমাস।
দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকারভেদঃ
দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমন:
১. মিলনার্থক শব্দযোগে: মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
২. বিরোধার্থক শব্দযোগে দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।
৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে আয়-ব্যয়, জমা-খচর, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি।
৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুন্ডু, নাক-মুখ ইত্যাদি।
৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে: সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি। যায়।
৬. সমার্থক শব্দযোগে হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।
৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধৃতি-চাদর ইত্যাদি।
৮. দুটি সর্বনামযোগে: যা-তা, যে-সে, যেমন-তেমন, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
৯. দুটি ক্রিয়াযোগে: দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া ইত্যাদি।
১০. দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে: ধীরে-সুস্থে, আগে-পাশে, আকারে-ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
১১. দুটি বিশেষণযোগে ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।
অলুক দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন: দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।
বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস: তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি।
দ্বিগু সমাস
সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।
বা, যে সমাসে প্রথম পদ সংখ্যা বা পরিমাপবাচক (যেমন: দুই, তিন, চার, বহু, অল্প, অধিক, একমুঠো, একপাত্র ইত্যাদি) হয় এবং সমাসবদ্ধ শব্দটি একবচন হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে।
যেমন:
১। দুই + পা = দ্বিপদী (দুই পা বিশিষ্ট)
২। তিন + নয়ন = ত্রিনয়ন (তিন চোখবিশিষ্ট (শিব))
৩। চার + ভুজ = চতুর্ভুজ (চার বাহুবিশিষ্ট)
৪। আট + ভুজ = অষ্টভুজ (আট বাহুবিশিষ্ট)
৫। এক + পাত্র = একপাত্র (একটি পাত্র)
৬। দুই + অর্থ + কথা = দ্ব্যর্থকথা (দ্ব্যর্থবোধক কথা)
৭। অল্প + বয়স = অল্পবয়সী (যার বয়স অল্প)
৮। অধিক + জন = অধিকজন (অধিক সংখ্যক ব্যক্তি)
৯। বহু + শ্রুত = বহুশ্রুত (অনেক কিছু শোনা)
১০। তিন + কাল = ত্রিকাল (তিন কালের সমাহার (ভবিষ্যৎ, বর্তমান, অতীত))
১১। শত + অব্দ = শতাব্দী (একশো বছরের সমাহার)
কর্মধারয় সমাস
যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।
বা, যে সমাসে প্রথম পদটি পরের পদের বিশেষণ, বিশেষ্য বা অব্যয় হয় এবং উভয় পদ মিলিয়ে একটি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠন করে, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।
যেমন:
১। নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম
২। মহৎ যে পুরুষ = মহাপুরুষ
৩। ভদ্র যে লোক = ভদ্রলোক
৪। সাদা যে পাথর = শ্বেতপাথর
৫। সোজা যে রেখা = সরলরেখা
৬। শান্ত যে স্বভাব = শান্তস্বভাব
৭। কাল যে পুরুষ = কালপুরুষ
৮। বুদ্ধি আছে যে ব্যক্তি = বুদ্ধিমান
৯। কৃষ্ণবর্ণ যে হরিণ = কৃষ্ণসার
১০। রাজার যে পুরুষ = রাজপুরুষ
কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ:
মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস: যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ।
উপমান কর্মধারয়ঃ সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র।
উপমিত কর্মধারয়: সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র।
রূপক কর্মধারয়: উপমান ও উপমেয় সমাসের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।
তৎপুরুষ সমাস
পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:
১। মন দিয়ে গড়া = মনগড়া
২। অবশ্যই প্রমাণিত = অবশ্যপ্রমাণিত
৩। প্রকৃত অবস্থান = প্রকৃতস্থান
৪। তথ্য দিয়ে সাজানো = তথ্যসজ্জিত
৫। অপরাধের শাস্তি = অপরাধশাস্তি
৬। খুব ভালো = খুবভাল
৭। প্রচলিত শব্দ = প্রচলিতশব্দ
৮। সহজেই বুঝতে পারা = সহজবোধ্য
৯। তাড়াতাড়ি আসা = তাড়াতাড়িকৃত
১০। নির্বাচিত ব্যক্তি = নির্বাচিতব্যক্তি
তৎপুরুষ সমাসের প্রকারভেদ:
দ্বিতীয়া তৎপুরুষ: পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।
তৃতীয়া তৎপুরুষ: পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয় তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখা।
অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ: পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি লোপ না হলে অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: তেলে ভাজা = তেলে ভাজা।
চতুর্থী তৎপুরুষ: পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: মেয়েদের জন্য স্কুল= মেয়েস্কুল।
পঞ্চমী তৎপুরুষ: পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত।
ষষ্ঠী তৎপুরুষ: পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: রাজার পুত্র = রাজপুত্র।
সপ্তমী তৎপুরুষ: পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ,য়, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: গাছে পাকা = গাছপাকা।
নঞ্চ তৎপুরুষ: না বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: ন আচার = অনাচার।
উপপদ তৎপুরুষ: কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয় তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন: পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ।
অলুক তৎপুরুষ: যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়ে ভাজা।
আরো পড়ুন:
বাংলা ব্যাকরণ পদ প্রকরণ, পদ কত প্রকার কি কি
বাংলা শব্দ ভান্ডার (সমার্থক শব্দ)
বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ
বহুব্রীহি সমাস
যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্যকোনো পদকে বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।
বা,যেখানে সমাসবদ্ধ শব্দটি কোনো একটি ব্যক্তি, বস্তুকে বোঝায়, কিন্তু সেই শব্দের অর্থ বা নাম সমাসে ব্যবহৃত পদদ্বয়ের মধ্যে নেই। অর্থাৎ, সমাসবদ্ধ শব্দটি অন্য কিছুকে নির্দেশ করে। যেমন:
১। মহান আত্মা যার = মহাত্মা
২। ত্রুটি যার মুখে = ত্রুটিমুখ
৩। ত্রিনয়ন যার = ত্রিনয়ন (শিব)
৪। চতুর্মুখ যার = চতুরানন (ব্রহ্মা)
৫। দুইবার জন্ম যার = দ্বিজ (ব্রাহ্মণ/পাখি)
৬। চাঁদের মতো মুখ যার = চন্দ্রমুখী
৭। অধিক কথা বলে যে = বাচাল
৮। অতি ধন যার = ধনতনয় (ধনী ব্যক্তি)
৯। চার পা যার = চতুষ্পদ (গরু/পশু)
১০। শত পদ যার = শতপদী (একধরনের কীট)
বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ:
সমানাধিকরণ বহুব্রীহি: পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন: খোশ মেজাজ যার = খোসমেজাজ।
ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি: বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয় তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি। যেমন: দুই কান কাটা যার = দু কানকাটা।
ব্যতিহার বহুব্রীহি: ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। যেমন: কানে কানে যে কথা = কানাকানি।
নঞ বহুব্রীহি: বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্চ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ বহুব্রীহি বলে। যেমন: নাই জ্ঞান যার = অজ্ঞান।
মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি: বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায় তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন: হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি।
প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি। যেমন: এক দিকে চোখ যার = একচোখা।
অলুক বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। যেমন: মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি।
সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি: পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। যেমন: দশ গজ পরিমাণ যার= দশগজি।
নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি: যে সমাস কোনো নিয়মের অধীনে নয় তাকে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি বলে। যেমন: দু দিকে অপযার দ্বীপ। জীবিত থেকেও যে মৃত= জীবস্মৃত।
অব্যয়ীভাব সমাস
পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অর্থাৎ, অব্যয় + বিশেষ্য / ক্রিয়া = অব্যয়ীভাব সমাস।
যেমন:
১। মরণ পর্যন্ত = আমরণ
২। জীবন ধরে = আজীবন
৩। তীক্ষ্ণভাবে হাসা = উপহাস
৪। চারপাশে ঘোরা = পরিক্রমা
৫। নির্দিষ্টভাবে বলা = নির্দেশ
৬। মিলিয়ে যোগ দেওয়া = সংযোগ
৭। বারবার ফেরা = প্রত্যাবর্তন
৮। চোখের কাছে আনা = উপনয়ন
৯। উপর বসবাস করা = অধিবাস
১০। সাজিয়ে রাখা = পরিপাটি
প্রাদি সমাস: প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎপ্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয় তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস। যেমন: প্র যে বচন = প্রবচন।
নিত্যসমাস: যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্যসমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না তাকে নিত্যসমাস বলে। যেমন: অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর।
বহুনির্বাচনী প্রশ্ন: সমাস কাকে বলে (নিজে কর)
১. সমাস কাকে বলে?
ক) একাধিক শব্দকে পৃথকভাবে বলা
খ) শব্দগুচ্ছের পরিণামে একটি শব্দ হওয়া
গ) শুধু উপসর্গ যুক্ত শব্দ
ঘ) একটি শব্দে দুইটি ক্রিয়া থাকা
২. “মাতাপিতা” কোন সমাস?
ক) দ্বন্দ্ব সমাস
খ) তৎপুরুষ সমাস
গ) বহুব্রীহি সমাস
ঘ) কর্মধারয় সমাস
৩. “ত্রিনয়ন” কোন সমাস?
ক) বহুব্রীহি
খ) দ্বিগু
গ) তৎপুরুষ
ঘ) কর্মধারয়
৪. “মহাত্মা” শব্দটি কোন সমাস?
ক) কর্মধারয়
খ) তৎপুরুষ
গ) বহুব্রীহি
ঘ) দ্বন্দ্ব
৫. “আমরণ” কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) তৎপুরুষ
খ) অব্যয়ীভাব
গ) দ্বিগু
ঘ) কর্মধারয়
৬. “গোশালা” শব্দে কতটি পদের সমাস হয়েছে?
ক) ৩টি
খ) ১টি
গ) ২টি
ঘ) ৪টি
৭. “দ্বিজ” শব্দের অর্থ কী?
ক) দুইবার মরা
খ) দুই চোখ আছে
গ) দুইবার জন্ম যার
ঘ) দুই ভাই
৮. “চন্দ্রমুখী” কোন সমাস?
ক) কর্মধারয়
খ) বহুব্রীহি
গ) তৎপুরুষ
ঘ) দ্বিগু
৯. “নীলপদ্ম” শব্দটি কোন সমাস?
ক) কর্মধারয়
খ) তৎপুরুষ
গ) দ্বন্দ্ব
ঘ) বহুব্রীহি
১০. নিচের কোনটি দ্বিগু সমাস নয়?
ক) ত্রিকাল
খ) শতাব্দী
গ) নীলকমল
ঘ) পঞ্চবটী
সমাস কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি? (Update) লেকচার শীট পিডিএফ ডাউনলোড কর।