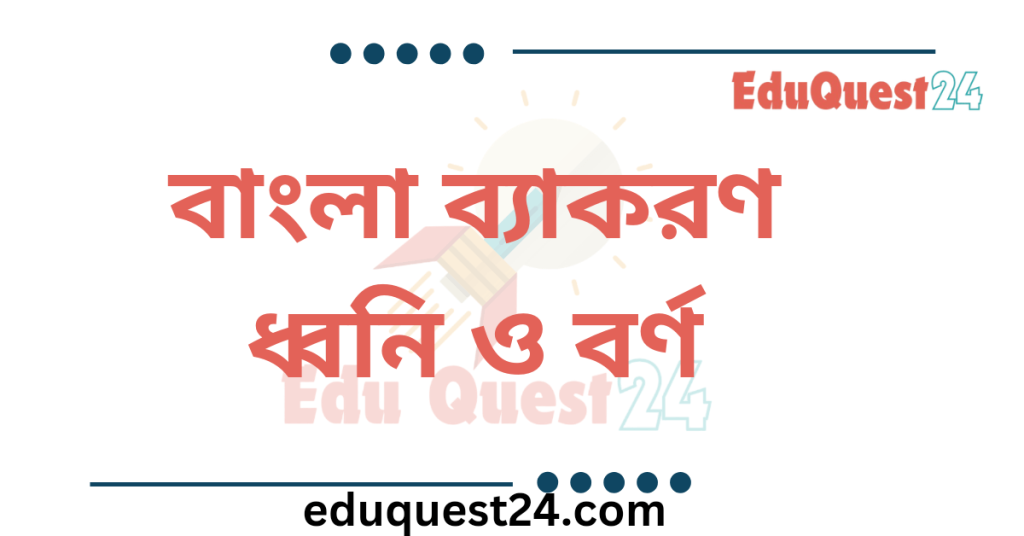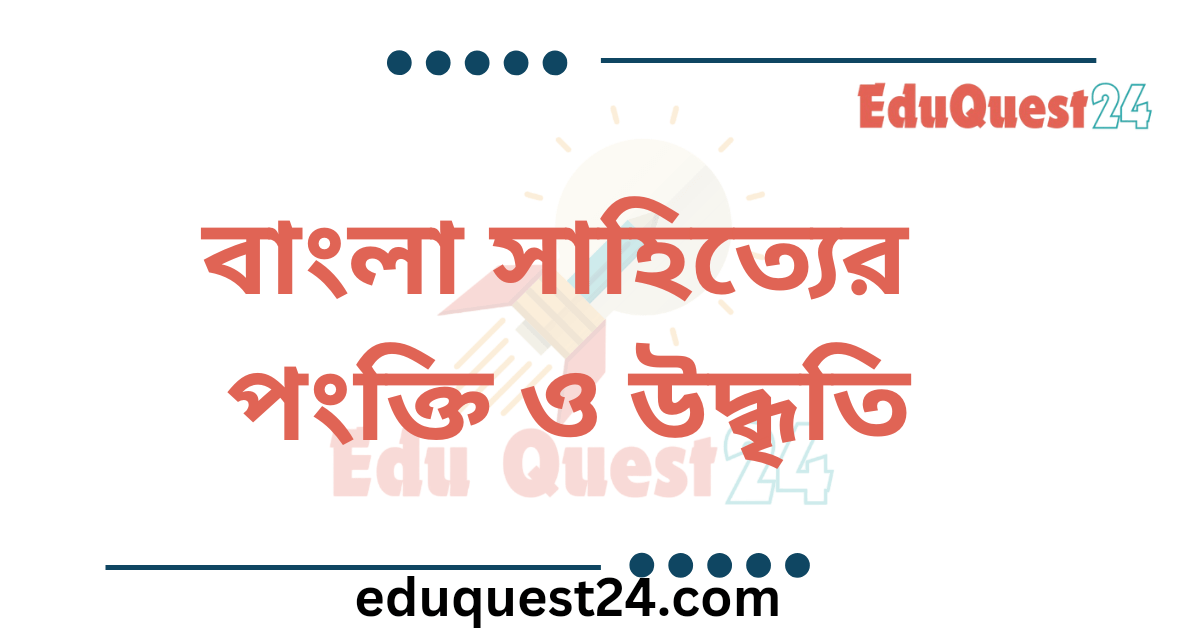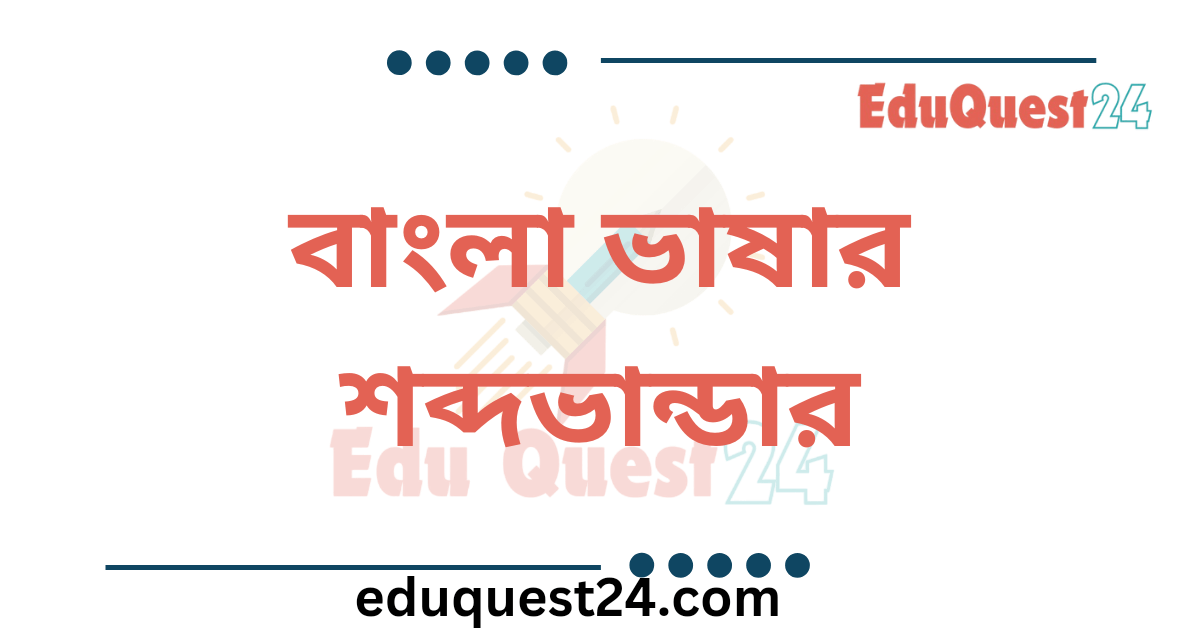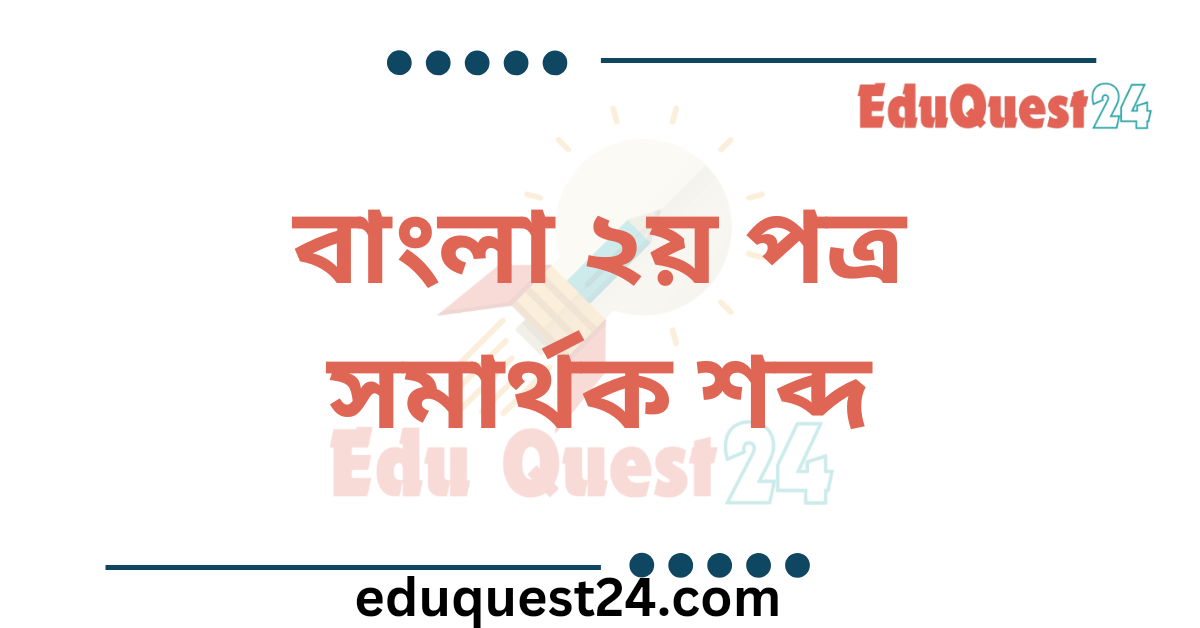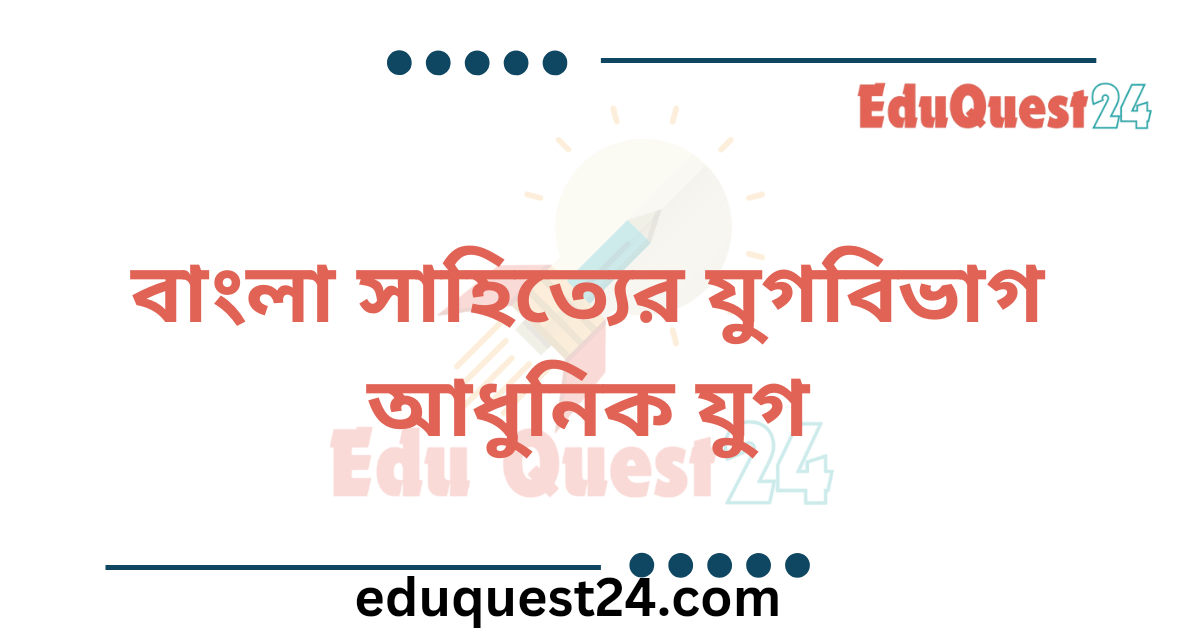বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ: বাংলা ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনি পরিবর্তন, বর্ণের গঠন এবং তাদের ব্যবহারের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে। বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনি কাঠামো এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাহলে চলো, শুরু করি।
বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ (PDF)
১। বর্ণঃ ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ।
২। স্বরবর্ণঃ স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ।
৩। ব্যঞ্জনবর্ণঃ ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ।
৪। বর্ণমালাঃ যে কোনো ভাষায় লিখিত বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় বর্ণমালা।
৫। বাংলা বর্ণমালায় বর্ণ আছে ৫০ টি।
৬। বাংলা বর্ণমালাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।
৭। স্বরবর্ণ আছে ১১টি।
৮। ব্যঞ্জনবর্ণ আছে ৩৯টি।
৯। মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ তিন প্রকার।
১০। মাত্রাহীন বর্ণঃ ১০টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ৪টি- এ, ঐ, ও, ঔ। ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি – ঙ, ঔ, ৎ, ঃ ,ঁ , ং।
১১। অর্ধমাত্রার বর্ণঃ ৮টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১টি ঋ। ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ।
১২। পূর্ণমাত্রার বর্ণঃ ৩২টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ৬টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি।
১৩। উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি ‘অ’ স্বরধ্বনি যুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়।
১৪। স্বরধ্বনি যুক্ত না হলে উচ্চারিত ব্যঞ্জনের নিচে হস্ বা হল চিহ্ন দিয়ে লিখতে হয়।
১৫। বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি রয়েছে ২৫টি।
১৬। কার: স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। বাংলায় ১০ টি কার রয়েছে।
১৭। ‘অ’ ছাড়া বাকি সব গুলো স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে।
১৮। স্বরবর্ণ যখন অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন কার ব্যবহৃত হয়।
১৯। ফলা: ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ফলা। বাংলায় ৬ টি ফলা রয়েছে।
২০। ৬টি ফলাঃ র-ফলা, ম-ফলা, ব-ফলা, য-ফলা, ল-ফলা, ন-ফলা।
২১।স্পর্শধ্বনি: ক থেকে ম পর্যন্ত। ২৫টি বর্ণকে স্পর্শধ্বনি বলা হয়।
• ক থেকে ৬ পর্যন্ত ক-বর্গীয় বর্ণ।
• চ থেকে ঞ পর্যন্ত চ-বর্গীয় বর্ণ।
• ত থেকে ন পর্যন্ত ত-বর্গীয় বর্ণ।
• ট থেকে ণ পর্যন্ত ট-বর্গীয় বর্ণ।
• প থেকে ম পর্যন্ত প-বর্গীয় বর্ণ।
২২। স্বরজ্ঞাপক বর্ণ: বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ রয়েছে ২টি। বর্ণ দুটি হলোঃ ঐ, ঔ।
২৩। যৌগিক স্বরধ্বনিকে দ্বি-স্বরও বলা হয়।
২৪। সংযুক্ত বর্ণ: দুটি বা তার বেশি বর্ণ যুক্ত হয়ে যখন শব্দ গঠিত হয়, তাকে সংযুক্ত বর্ণ বলে।
২৫। বাংলা ভাষায় তিন ভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হতে পারে।
২৬। বাংলা ভাষায় শিশ বর্ণ ৩ টি। যথাঃ শ, ষ, স।
২৭। বাংলা ভাষায় উষ্মবর্ণ ৪ টি। যথাঃ শ, ষ, স, হ।
২৮। সকল শিশ বর্ণই উষ্মবর্ণ কিন্তু সকল উষ্ম বর্ণ শিশ বর্ণ নয়।
২৯। নাসিক্য বর্ণ ৭টি। যথাঃ ঙ, ঞ, ম, ন, ণ, (ং)।
৩০। পৃথক উচ্চারণ নেইঃ ন, ণ, ঙ, (ং)।
৩১। পরাশ্রয়ী বর্ণ ৩ টি – ৎ, ং, ঁ।
৩২। তাড়িত ধ্বনি/ তাড়নজাত বর্ণ ২ টি (ড়, ঢ়)।
৩৩। কম্পিত ধ্বনি/ কম্পনজাত বর্ণ ১ টি (র)।
৩৪। অন্তঃস্থ বর্ণ ৪ টি (য, র, ল, ব) ।
৩৫। অন্তঃস্থ ধ্বনি ৩ টি (র, ল, ব)।
৩৬। অযোগবাহ বর্ণ ২ টি (ংঃ)। বর্ণ অতিরিক্ত চিহ্ন ২ টি (হসন্ত, রেফ)।
৩৭। ধ্বনিঃ কোনো ভাষার বাকপ্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি / Sound পাই। বাংলা ভাষাতেও কতগুলো মৌলিক ধ্বনি আছে। বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন: স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।
৩৮। স্বরধ্বনি: যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না তাদের বলা হয় স্বরধ্বনি / Vowel sound। যেমন: অ, আ, ই, উ, ঊ ইত্যাদি।
৩৯। ব্যঞ্জনধ্বনি: যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে তাদের বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি / Consonant sound। যেমন: ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।
বাংলা ভাষার বর্ণ প্রকরণ (ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ)
৪০। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ/ Letter। বর্ণ দুই প্রকার। যেমন: স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।
৪১। স্বরবর্ণঃ স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন: অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।
৪২। ব্যঞ্জনবর্ণঃ ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন : ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি।
৪৩। বর্ণমালাঃ যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা / Alpha-bet বলা হয়।
৪৪। বঙ্গলিপিঃ যে বর্ণমালায় বাংলা ভাষা লিখিত হয় তাকে বলা হয় বঙ্গলিপি।
[বিশেষ দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য: উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি ‘অ’ স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন: ক্+অ=ক। স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের নিচে ‘হস্’ বা ‘হল’ চিহ্ন (৫) দিয়ে লিখিত হয়। এরূপ বর্ণকে বলা হয় হসন্ত বা হসন্ত বর্ণ।]
বাংলা বর্ণমালা (ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ)
৪৫। বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ ১১ টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি।
৪৬। স্বরবর্ণ: অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ । ১১টি
৪৭। ব্যঞ্জনবর্ণ:
• ক খ গ ঘ ঙ (ক-বর্গ) ৫টি
• চ ছ জ ঝ ঞ (চ-বর্গ) ৫টি
• ট ঠ ড ঢ ণ (ট-বর্গ) ৫টি
• ত থ দ ধ ন (ত-বর্গ) ৫টি
• প ফ ব ভ ম (প-বর্গ) ৫টি
• য র ল ৩টি
• শ ষ স হ ৪টি
• ড় ঢ় য় ৎ ৪টি
• ৎ ং ঁ ৩টি
[বিশেষ দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য: ‘ঐ, ঔ’ দুটি দ্বি-স্বর বা যুগ্ম স্বরধ্বনির প্রতীক। যেমন: অই (অ+ই/ও+ই), ঔ (অ+উ/ও+উ)।]
৪৮। বর্গীয় বর্ণ ২৫টি। ক খ গ ঘ ঙ/ চ ছ জ ঝ ঞ /ট ঠ ড ঢ ণ/ ত থ দ ধ ন/ প ফ ব ভ ম
৪৯। কার ৯টি। আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ
৫০। ফলা ৬টি। ন-ফলা, ম- ফলা, ব-ফলা, য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা
৫১। অল্পপ্রাণ স্বরবর্ণ ৫টি। অ ই উ এ ও
৫২। মহাপ্রাণ স্বরবর্ণ ৫টি। আ ঈ ঊ ঐ ঔ
৫৩। অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণ ২৪টি। ক গ ঙ/চ জ ঞ/ট ড ণ/ত দ ন/প ব ম/য র ল শ/ষ স ড়, য়/ঃ (উচ্চারণ-বর্ণ+অ)
৫৪। মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণ ১১টি। খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ ঢ় (উচ্চারণ-বর্ণ+অহ)
৫৫। পূর্ণমাত্রা স্বরবর্ণ ৬টি। অ আ ই ঈ উ উ
৫৬। মাত্রাহীন স্বরবর্ণ ৪টি। এ ঐ ও ঔ
৫৭। মৌলিক স্বরবর্ণ ৮টি। অ আ ই ঈ উ উ এ ও
৫৮। মৌলিক স্বরবর্ণ ২টি। ঐ (অ/ও+ই), ঔ (অ/ও+উ)
৫৯। পূর্ণমাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি। ক ঘ/চ ছ জ ঝ/ট ঠ ড ঢ/ত দ ন/ফ ব ভ ম/য র ল ষ/স হ ড় ঢ় য়
৬০। অধমাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি। খ গ ণ থ ধ প শ
৬১। মাত্রাহীন ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি। ঙ ঞ ং ঁ ৎ ঃ
৬২। আশ্রিত বর্ণ ৩টি। ং ঁ ঃ
৬৩। নাসক্যি বর্ণ/অনুনাসকি ৭টি। ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ঁ, ঃ
৬৪। দ্বিস্বর/যৌগিক স্বর ২৫টি।
৬৫। যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ২টি। ঐ, ঔ
৬৬। স্পশ ব্যঞ্জন ২৫টি। ক-ম পর্যন্ত
৬৭। উষ্মধ্বনি ৪টি। শ, ষ, স, হ
স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ (ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ)
৬৮। কার: স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে।
৬৯। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন: অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। এই রূপ বা form শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত-যে কোনো অবস্থানে বসতে পারে।
৭০। স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয় তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত স্বর বা ‘কার’। যেমন: ‘আ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ (া)। ‘ম’-এর সঙ্গে ‘আ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ ‘তা’ যুক্ত হয়ে হয় ‘মা’। বানান করার সময় বলা হয় ম-এ আ-কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়।
৭১। অ-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা ‘কার’ নাই।
৭২। স্বর বা কার ব্যঞ্জনবর্ণের যেখানে যুক্ত হয়:
• ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয় আ-কার, ঈ-কার। যেমন: মা, মী,
• ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয় ই-কার, এ-কার, ঐ-কার। যেমন: মি, মে, মৈ,
• ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়: উ-কার, উ-কার, ঋ-কার। যেমন: মু, মু, মৃ,
• ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিকে যুক্ত হয় ও-কার, ঔ-কার। যেমন: মো, মৌ
৭৩। বর্গীয় ধ্বনিঃ ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শধ্বনিকে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি গুচ্ছে বা বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ঐ বর্গীয় ধ্বনি।
৭৪। বর্গভুক্ত বলে এ ধ্বনির প্রতীকগুলোও ঐ বর্গীয় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন:
• ক খ গ ঘ ঙ ধ্বনি হিসেবে এগুলো কণ্ঠ্য ধ্বনি
• চ ছ জ ঝ ঞ ধ্বনি হিসেবে এগুলো তালব্য ধ্বনি
• ট ঠ ড ঢ ণ ধ্বনি হিসেবে এগুলো মূর্ধন্য ধ্বনি
• ত থ দ ধ ন ধ্বনি হিসেবে এগুলো দন্ত্য ধ্বনি
• প ফ ব ভ ম ধ্বনি হিসেবে এগুলো ওষ্ঠ্য ধ্বনি
৭৫। ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক জিহ্বা ও ওষ্ঠ্য। আর উচ্চারণের স্থান হলো কণ্ঠ বা জিহ্বামূল অগ্রতালু, মূর্ধা বা পশ্চাৎ দন্তমূল, দন্ত বা অগ্র দন্তমূল, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি।
৭৬। উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:
- কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয়
- তালব্য বা অগ্রতালুজাত
- মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়
- দন্ত্য বা অগ্র দন্তমূলীয়
- ওষ্ঠ্য
৭৭। মোট বাগযন্ত্র (১২টি)। যথা:
- ঠোঁট, ওষ্ঠ্য
- দাঁতের পাটি
- দন্তমূল, অগ্র দন্তমূল
- অগ্রতালু, শক্ত তালু
- পশ্চাৎতালু, নরম তালু, মূর্ধা
- আলজিহ্বা
- জিহ্বাগ্র
- সম্মুখ জিহ্বা
- পশ্চাদজিহ্বা, জিহ্বামূল
- নাসা-গহ্বর
- স্বর-পল্লব, স্বরতন্ত্রী
- ফুসফুস
৭৮। যৌগিক স্বর: পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর, সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষর বা দ্বি-স্বর বলা হয়। যেমন:
• অ+ই=অই (উন)
• অ+উ+অউ (বউ)
• অ+এ-অয়, (বয়, ময়না)
• অ+ও+অও (হও, লও)
৭৯। বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ:
• আ-ই-আই (যাই, ভাই)
• আ+উ=আউ (লাউ)
• আ+এ-আয় (যায়, খায়)
• আ+ও-আও (যাও, খাও)
• ই+ই-ইই (দিই)
• ই+উ-ইউ (শিউলি)
• ই+এ-ইয়ে (বিয়ে)
• ই+ও-ইও (নিও, দিও)
• উ+ই-উই (উই, শুই)
• উ+আ=উয়া (কুয়া)
• এ+আ=এয়া (কেয়া, দেয়া)
• এ+ই-এই (সেই, নাই)
• এ+ও-এও (খেও)
• ও-ও-ওও (শোও)
৮০। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে। যেমন: ঐ (কৈ), ও (বৌ)। অন্য যৌগিক স্বরের প্রতীক স্বরূপ কোনো বর্ণ নাই।
৮১। স্পর্শ ব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি: পাঁচটি বর্ণ বা গুচ্ছে প্রত্যেকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলো স্পৃষ্ট ধ্বনিজ্ঞাপক। ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনকে স্পর্শ ব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
৮২। উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্পর্শ ব্যঞ্জনকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: অঘোষ ও ঘোষ।
• অঘোষ ধ্বনিঃ যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না তাকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। যেমন: ক, খ, চ, ছ।
• ঘোষ ধ্বনিঃ যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় তাকে বলে ঘোষ ধ্বনি। যেমন: গ, ঘ, জ, ঝ।
৮৩। শ, ষ, স, হ-চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এদের বলা হয় উষ্মধ্বনি। শ ষ স-তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ
৮৪। অল্পপ্রাণ আর ‘হ’ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।
৮৫। য/ Y, ব্ / W-দুটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মাঝামাঝি। এজন্য এদের বলা হয় অন্তঃস্থ ধ্বনি। আর বর্ণ দুটিকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।
৮৬। ই, ঈ ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা এগিয়ে আসে, উচ্চে অগ্রতালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পৌঁছে।
৮৭। ‘এ’ মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি এবং ‘অ’ নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি।
৮৯। ‘উ’, ‘ঊ’ ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে এবং পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলা হয়।
৯০। ‘উ’, ‘ঊ’ ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চে থাকে বলে এদের বলা হয় উচ্চ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ও মধ্যাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি এবং অ-নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।
৯১। বাংলা আ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থ অংশে অবস্থিত বলে আ-কে কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি এবং বিবৃত ধ্বনিও বলা হয়।
৯২। বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলোঃ (স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান ৭টি) শব্দে অবস্থানভেদে ‘অ’ দুইভাবে লিখিত হয়। যেমন:
• স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন: অমর, অনেক।
• শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন: কর, বল। এখানে কওর আর বওল বর্ণের সঙ্গে অ বিলীন হয়ে আছে। (ক্+অর্++অ; ব্+অ+ল্+অ)।
৯৩। শব্দের অ-ধ্বনির দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়। যথা:
• বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন: অমল, অনেক, কত।
• সংবৃত বা ও-ধ্বনির মতো উচ্চারণ। যেমন: অধীর, অতুল, মন। এ উচ্চারণগুলোতে অ-এর উচ্চারণ অনেকটা ও-এর মতো (ওধীর, ওতুল, মোন)।
‘অ’-ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণঃ ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ
• শব্দের আদিতে না-বোধক ‘অ’ যেমন: অটল, অনাচার।
• ‘অ’ কিংবা ‘আ’-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন: অমানিশা, অনাচার, কথা।
শব্দের মধ্যে ও অন্তেঃ
• পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত ‘অ’। যেমন: কলম, বৈধতা, যত, শ্রেয়ঃ।
• ঋ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি, ঐ-ধ্বনি এবং ঔ-ধ্বনির পরবর্তী ‘অ’ প্রায়ই বিবৃত হয়। যেমন: তৃণ, দেব, বৈধ, নোলক, মৌন। অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন: গঠিত, মিত, জনিত ইত্যাদি।
[বিশেষ জ্ঞাতব্য বা দ্রষ্টব্য: বাংলায় ঋ-ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।]
এ-ধ্বনির উচ্চারণ (ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ)
এ-ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম: সংবৃত ও বিবৃত। যেমন: মেঘ (সংবৃত), খেলা (খ্যালা), (বিবৃত)।
সংবৃতঃ
• পদের অন্তে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন: পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে, আসে ইত্যাদি।
• তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন: দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।
• একাক্ষর সর্বনাম পদের ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন: কে, সে, যে।
• ‘হ’ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন: দেহ, কেহ, কেষ্ট।
• ‘ই’ বা ‘উ’-কার পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন: দেখি, রেণু, বেলুন।
বিবৃতঃ
• ‘এ’ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট/ cat ও ব্যাট/ bat -এর ‘এ’ /ধ-এর মতো। যেমন: দেখ (দ্যাখ), একা (এ্যাকা) ইত্যাদি।
• ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।
• দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে। যেমন: এত, হেন, কেন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম-যেমন, সেথা, হেথা।
• অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগের ধ্বনি বিবৃত। যেমন: খেংড়া, চেংড়া, স্যাঁতসেঁতে, গেঁজেল।
• খাঁটি বাংলা শব্দ। যেমন: খেমটা, ঢেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।
• এক, এগার, তের কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে। ‘এক’ যুক্ত শব্দেও। যেমন: একচোট, একতলা, একঘরে ইত্যাদি।
• ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়, তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপে। যেমন : দেখ (দ্যাখ), দেখ (দ্যাখো), খেল্ (খ্যাল), খেল (খ্যালো), ফেল (ফ্যাল), ফেল (ফ্যালো) ইত্যাদি।
• ‘ঐ’: ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ+ই কিংবা ও+ই=অই, ওই।
ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ (ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ)
• ক-বর্গীয় ধ্বনি: ক, খ, গ, ঘ, ঙ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি।
• চ-বর্গীয় ধ্বনি: চ, ছ, জ, ঝ, ঞ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপ্টাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।
• ট-বর্গীয় ধ্বনি: ট, ঠ, ড, ঢ, ণ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টা হয় বলে এদের নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। আবার এগুলো ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় মূর্ধন্য ধ্বনি।
• ত-বর্গীয় ধ্বনি: ত, থ, দ, ধ, ন পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি।
• প-বর্গীয় ধ্বনি: প, ফ, ব, ভ, ম পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলে।
আরো পড়ুন:
- বাংলা ভাষার (ব্যাকরণ) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- বাংলা সাহিত্যের পংক্তি ও উদ্ধৃতি (উক্তি)
- বাংলার কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ও উপাধি
- বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম
অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ (ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ)
স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণরীতির দিক থেকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ, অঘোষ ও ঘোষ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়।
- অল্পপ্রাণ ধ্বনি: কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি / Unaspirated যেমন: ক, গ ইত্যাদি।
- মহাপ্রাণ ধ্বনি: কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি / Unaspirated যেমন: খ, ঘ ইত্যাদি।
ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির উচ্চারণ (ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ)
• অঘোষ ধ্বনি: কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গাম্ভীর্যহীন ও মৃদু হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি / Un-voiced যেমন: ক, খ ইত্যাদি।
• ঘোষ ধ্বনি: ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি / Voiced হয়। যেমন: গ, ঘ ইত্যাদি।
অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলো নিচের ছকে দেখানো হলো:
অন্তঃস্থ ধ্বনির উচ্চারণ (ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ)
• অন্তঃস্থ ধ্বনি: স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে ‘যরলব’ ইত্যাদি ধ্বনিকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।
• য: য বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি সাধারণত সম্মুখ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এজন্য ধ্বনিটিকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে বাংলায় এর উচ্চারণ ‘জ’ এর মতো হয়। যেমন: যখন, যাবেন, যুদ্ধ, যম ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে ‘য়’ উচ্চারিত হয়। যেমন: বি+যোগ-বিয়োগ।
• র: র বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তা দ্বারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলে ধ্বনিটিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়। যেমন: রাহাত, আরাম, বাজার।
• ল: ল বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেয়া হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন: লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।
• ব: বাংলা বর্ণমালায় বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্ব-ব এদের আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই। আগে বর্গীয় ও ‘অন্তঃস্থ-ব’ দুই রকমের ‘ব’ লেখার আকৃতিও পৃথক ছিল এবং উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বলে ‘অন্তঃস্থ-ব’কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্তস্থ ‘য’ ও অন্তঃস্থ ‘ব’ দুটি অর্ধস্বর /Semivowel এর প্রথমটি অয় বা ইয় (y) এবং দ্বিতীয়টি অব বা অও (w)-র মতো। যেমন: নেওয়া, হওয়া ইত্যাদি।
উষ্মধ্বনির উচ্চারণ (ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ)
• উষ্মধ্বনি: যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিশধ্বনির সৃষ্টি করে সেটি উষ্মধ্বনি। যেমন: আশীষ, শিশি, শিশু ইত্যাদি। শিশ দেয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে বলে একে শিশধ্বনিও বলা হয়।
• উষ্ম বর্ণ: শ, ষ, স তিনটি উষ্ম বর্ণ। ‘শ’ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান পশ্চাৎ দন্তমূল। ‘ষ’ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং ‘স’ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান দন্ত।
• লক্ষণীয়: স-এর সঙ্গে খর তথ কিংবা ন যুক্ত হলে স-এর দন্ত্য উচ্চারণ হয়। যেমন: স্খলন, স্রষ্টা, আস্ত, স্থাপন, স্নেহ ইত্যাদি। আবার বানানে (লেখায়) শ থাকলেও উচ্চারণ দন্ত্য-স হয়। যেমন: শ্রমিক (শ্রমিক), শৃঙ্খল (সৃঙ্খল)।
• ড়, গাঢ়, রাহ: হ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন মূল উষ্ম ঘোষধ্বনি। উষ্মধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্মুক্ত কণ্ঠে মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। যেমন : হাত, মহা, পহেলা ইত্যাদি।
• ং অনুস্বার: ০ং উচ্চারণ ঙ উচ্চারণের মতো। যেমন: রং (রঙ), বাংলা (বাঙলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায়ং বদলে ঙ আবার ঙ বদলে ০ং ব্যবহার খুবই সাধারণ।
• ঃ বিসর্গ: বিসর্গ হলো অঘোষ ‘হ’ উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। হ উচ্চারণ ঘোষ কিন্তু ০ঃ উচ্চারণ অঘোষ। বাংলায় একমাত্র বিস্বয়াদি প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যেমন: আঃ, উঃ, ওঃ, বাঃ ইত্যাদি। সাধারণত বাংলায় শব্দের অন্তে বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। যেমন: বিশেষতঃ (বিশেষত), ফলতঃ (ফলত)। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন: দুঃখ (দুখ), প্রাতঃকাল (প্রাতক্কাল)।
• ড়, ঢ়ঃ ড়, ঢ় বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় তাড়নজাত ধ্বনি। ড় উচ্চারণ ড, র দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মাঝামাঝি এবং ঢ় উচ্চারণ ড়, হ দ্বারা দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের দ্রুত মিলিত ধ্বনি। যেমন: বঢ় ইত্যাদি।
• দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি বা অধিক একত্রে উচ্চারিত হয়। এরূপ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটি বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ / ligature গঠিত হয়। সাধারণত এরূপে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন: তক্তা (ত্+অ+ক্+ত্+আ=তক্তা)। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত-এর মূলরূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ত হয়েছে।
১০১। দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে অর্থবোধক ধ্বনি সৃষ্টি করলে যুক্তবর্ণ হয়। অথবা অ’র হসোচ্চারণ নিতেই ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনের অর্থপূর্ণ যুক্ত অবস্থানকে যুক্তবর্ণ :
ধ্বনির পরিবর্তনঃ ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ
১০২। বর্গীয় ধ্বনিঃ ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শধ্বনিকে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি গুচ্ছে বা বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ঐ বর্গীয় ধ্বনি। বর্গভুক্ত বলে এ ধ্বনির প্রতীকগুলোও ঐ বর্গীয় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন:
১০৩। আদি স্বরাগম / Prothesis: উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগম। যেমন: স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন ইস্টিশন। এরূপ: আস্তাবল, আস্পর্ধা।
১০৪। মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি / Anaptyxis: সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন:
• অ: রত্ন-রতন, ধর্ম>ধরম, স্বপ্ন স্বপন, হর্ষ হরষ ইত্যাদি।
• ই: প্রীতি>পিরীতি, ক্লিপ>কিলিপ, ফিল্ম ফিলিম ইত্যাদি।
• উ: মুক্তা>মুকুতা, তুর্ক তুরুক, ভ্রু-ভুরু ইত্যাদি।
• এ: গ্রাম>গেরাম, প্রেক>পেরেক, স্রেফ সেরেফ ইত্যাদি।
• ও: শ্লোক-শোলোক, মুরগ>মুরোগ>মোরগ ইত্যাদি।
১০৫। অন্ত্যস্বরাগম / Apothesis: কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমন: দিশ দিশা, পোখত পোক্ত, বেঞ্চ বেঞ্চি, সত্য>সত্যি ইত্যাদি।
১০৬। অপিনিহিতি: পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন: আজি>আইজ, সাধু সাউধ, রাখিয়া রাইখ্যা, বাক্য>বাইক্য, সত্য>সইত্য, চারি>চাইর, মারি মাইর।
১০৭। অসমীকরণ: একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন: ধপ ধপ ধপাধপ, টপটপ টপাটপ।
১০৮। স্বরসঙ্গতি: একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন: দেশি>দিশি, বিলাতি>বিলিতি, মুলা>মুলো।
• প্রগত স্বরসঙ্গতি: আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন: মূল্য মূলো, শিকা>শিকে, তুলা তুলো।
• পরাগত স্বরসঙ্গতি: অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন: আখো> আখুয়া> এখো, দেশি> দিশি।
• মধ্যগত স্বরসঙ্গতি: আদ্যস্তর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন: বিলাতি>বিলিতি।
• অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন: মোজা> মুজো।
১০৯। সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ: দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন: বসতি>বসইত, জানালা জাল্লা ইত্যাদি।
• আদিস্বরলোপ / Aphesis: যেমন: অলাবু>লাবু>লাউ, উদ্ধার>উধার>ধার।
• মধ্যস্বর লোপ / Syncope: অগুরু অগ্র, সুবর্ণ স্বর্ণ।
• অন্ত্যস্বর লোপ / Apocope: আশা আশ, আজি>আজ, চারি-চার (বাংলা), সন্ধ্যা>সঞঝা-সাঁঝ।
১১০। ধ্বনি বিপর্যয়: শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন: ইংরেজি বাক্স বাংলা বাস্ক, জাপানি রিক্সা>বাংলা রিস্কা ইত্যাদি। অনুরূপ-পিশাচ-পিচাশ, লাফ>ফাল।
১১১। সমীভবন: শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমন: জন্ম-জন্ম, কাঁদনা কান্না ইত্যাদি।
• প্রগত সমীভবন: পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন। যেমন: চক্র>চক্ক, পকৃ>পক্ক, পদ্ম>পদ্দ, লগ্ন লগ্ন ইত্যাদি।
• পরাগত সমীভবন: পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয় একে বলে পরাগত সমীভবন। যেমন: তৎ+জন্য তজ্জন্য, তৎ+হিত তদ্ধিত, উৎ+মুখ উন্মুখ ইত্যাদি।
• অন্যোন্য সমীভবন: যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীভবন। যেমন: সংস্কৃত সত্য>প্রাকৃত-সচ্চ, সংস্কৃত-বিদ্যা-প্রাকৃত-বিজ্জা ইত্যাদি।
১১২। বিষমীভবন: দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন: শরীর শরীল, লাল>নাল।
১১৩। দ্বিত্ব ব্যঞ্জন: কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব। যেমন: পাকা পাক্কা, সকাল সক্কাল ইত্যাদি। ব্যঞ্জন বিকৃতি: শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন: কবাট-কপাট, ধোবা>ধোপা, ধাইমা-লাইমা ইত্যাদি।
১১৪। ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি: পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমন: বউদিদি বউদি, বড় দাদা-বড়দা ইত্যাদি।
১১৫। অন্তর্হতিঃ পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন: ফাল্গুন ফাগুন, ফলাহার> ফলার, আলাহিদা আলাদা ইত্যাদি।
১১৬। অভিশ্রুতি: বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি। যেমন করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে ‘কইরিয়া’ কিংবা বিপর্যয়ের ফলে ‘কইরা’ থেকে অভিশ্রুতিজাত ‘করে’। এরূপ: শুনিয়া> শুনে, বলিয়া>বলে, হাটুয়া হাউটা>হেটো, মাছুয়া>মেছো ইত্যাদি। আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন: তর্ক-তক্ক, করতে>কত্তে, মারল>মাল্ল, করলাম-কল্লাম।
১১৭। আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন: পুরোহিত পুরুত, গাহিল-গাইল, চাহে চায়, সাধু-সাহু-সাউ, আরবি-আল্লাহ>বাংলা-আল্লা, ফারসি-শাহ্-বাংলা-শা ইত্যাদি।
১১৮। শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর (যৌগিক স্বর) না হয় তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ ‘য়’ (ণ) বা অন্তঃস্থ ‘ব’ (ড) উচ্চারিত হয়।
বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ (শ্রেণীবিভাগ) | বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ বিসিএস লেকচার শীট ডাউনলোড কর।